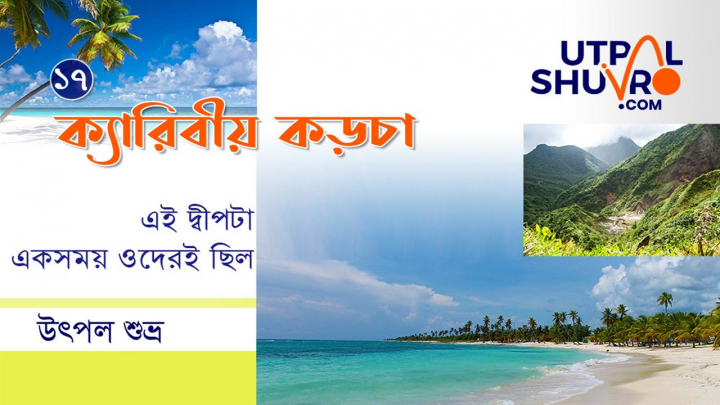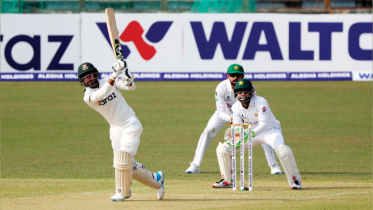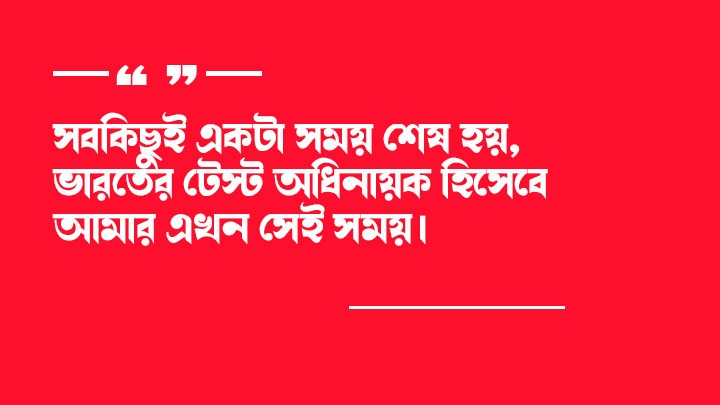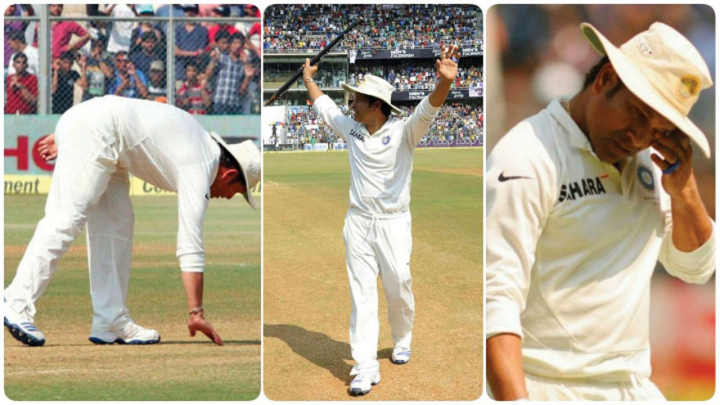এই দ্বীপটা একসময় ওদেরই ছিল
ডমিনিকায় গেলে `বয়লিং লেক` দেখাটা নাকি অবশ্য দ্রষ্টব্যের মধ্যেই পড়ে। কিন্তু সারা দিনের হ্যাপা বলে বাদ দিয়েছিলাম ওখানে যাওয়ার পরিকল্পনা। ঘুরে বেড়ালাম ডমিনিকার রাজধানী রজো, দেখা হলো ক্যারাবিয়ানের আদি বাসিন্দা কারিবদের সঙ্গে। যারা অবশ্য অতীতের সেসব দিন পেছনে ফেলে এখন যথেষ্টই আধুনিক।
প্রথম প্রকাশ: ২৯ জুলাই ২০০৯। প্রথম আলো।
‘বয়লিং লেক’ দেখতে চেয়েছিলাম। ডমিনিকায় পর্যটকদের অবশ্য দ্রষ্টব্যের মধ্যে এটা নাকি এক নম্বর। লাখ লাখ বছর আগে সাগরের তলায় অগ্ন্যুৎপাত থেকে জন্ম এই দ্বীপের। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম ওই ফুটন্ত লেক (সবচেয়ে বড়টা নিউজিল্যান্ডের রটোরুয়াতে) এখনো যার চিহ্ন হয়ে বাষ্প ছড়িয়ে যাচ্ছে।
খোঁজখবর করে তো হতভম্ব। ওটি দেখতে গাড়িতে ঘণ্টাখানেক। যাওয়ার পর তিন ঘণ্টা নাকি পাহাড়ি পথ বেয়ে উঠতে হয়। নামতে আবার তিন ঘণ্টা। এ তো সারা দিনের ব্যাপার! বিশ্রামের জন্য পরের দিনটাও বরাদ্দ রাখতে হবে। বয়লিং লেক প্রকল্প তাই বাদ। কিন্তু তাহলে করবটা কী?
ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠতে হওয়া যদি ওয়েস্ট ইন্ডিজ ট্যুর করতে আসার বড় যন্ত্রণা হয়, মুদ্রার অন্য পিঠে আছে খেলা না থাকার দিনগুলোতে বেলা ১১টা-১২টার মধ্যে ফ্রি হয়ে যাওয়ার আনন্দ। ১১ ঘণ্টা সময় পার্থক্যের কারণে যা লেখার তা তো ওই সময়ের মধ্যেই লিখতে হয়।
পরশু লেখা-টেখা শেষ করে সামনে পুরো একটা দিন। একবার ভাবলাম, জলপ্রপাত দেখে আসি। সেদিনও হোটেলের এক লোক ট্রাফালগার জলপ্রপাতের কথা খুব বলল। ভেবেচিন্তে সেই পরিকল্পনাও বাতিল। দুবার ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত দেখার পর নায়াগ্রা ছাড়া আর কোনো জলপ্রপাত দেখতে গেলে সেটিকে অপমান করা হয়। আমি তাই কিছুক্ষণ উদ্দেশ্যহীন শহরে ঘুরে বেড়ােব বলে ঠিক করলাম।

সেটি আর কতক্ষণ? আগেই বোধ হয় জানিয়েছি, ডমিনিকার রাজধানী শহর রজো পায়ে হেঁটেও মিনিট বিশেকের মধ্যে চক্কর দিয়ে দেওয়া যায়। মলিন সব দোকানপাট। রাস্তায় পার্কিং করে রাখা গাড়ি আর গাড়ি। গাড়ি ছাড়া নাকি এই দেশে চলা প্রায় অসম্ভব। সব রাস্তাই ওয়ানওয়ে। তের বছর ধরে ডামিনিকাবাসী বাংলাদেশি বদরুজ্জামানের কাছ থেকে জেনেছি, রাস্তায় কোনো ট্রাফিক পুলিশের দেখা না মিললেও ট্রাফিক আইন এখানে খুব কঠোর। অননুমোদিত জায়গায় গাড়ি পার্কিং করলেই মোটা অঙ্কের জরিমানা। না দিলে জেলহাজত। সব রাস্তার দুই পাশেই পার্কিং করা গাড়ির মিছিল দেখে সব জায়গাই অনুমোদিত বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক।
রাস্তা হারিয়ে ফেলায় আমার বিশেষ সুনাম আছে। এই ছোট্ট রজোতেও আমি তা ধরে রাখতে সক্ষম হলাম। এ দোকান-সে দোকানে ঢুঁ মারছি, হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলাম তরিতরকারির বাজারে। ক্যারিবিয়ানের অন্য দ্বীপগুলোর সঙ্গে ব্যতিক্রম হয়ে ডমিনিকার অর্থনীতির পর্যটনের কাছাকাছিই কৃষির ওপর নির্ভরতা। তরিতরকারি-ফলমূল প্রচুর হয়। বাজারে আঙুলের মতো চিকন চিকন গাজর দেখলাম, বেগুন-টমেটো, রান্না করে খেতে হয় এমন বিশাল বিশাল কলা। সবচেয়ে বেশি দেখলাম বাঁধাকপি। ফুলকপি নাকি এখানে হয় না। আমেরিকা থেকে কিছু আমদানি হয়, সেগুলোর আকাশছোঁয়া দাম।
তরকারির বাজারে দরদাম করে (বিদেশি মুদ্রার বিনিময় হারের কারণে মুদ্রাস্ফীতির বাংলাদেশও এখানকার তুলনায় অনেক সস্তা) হোটেলে ফিরব, আর পথ খুঁজে পাই না। এটুকু শহর হাঁটতে হাঁটতেই পেয়ে যাব ভেবে একটু এগোতেই থমকে গেলাম একটা সাইনবোর্ড দেখে। 'কারিব-টারিব' কী যেন লেখা। ভেতরে ঢুকে দেখলাম, এটাও জাদুঘরের মতোই। ক্যারিবিয়ানের আদি বাসিন্দা কারিবদের হাজার বছরের সব নিদর্শন। যাক, রাস্তা ভুল করে ভালোই হয়েছে। কারিবদের আদি চিহ্ন-টিহ্ন দেখি। সেন্ট ভিনসেন্টে কারিব বংশোদ্ভূত ট্যাক্সিচালকের সঙ্গে পরিচয়ের পর থেকে কারিবদের নিয়ে আমার খুব আগ্রহ জন্মেছে।
ক্যারিবিয়ান সাগরের নামটা ‘কারিব’ থেকেই এসেছে। ইংরেজি ক্যানিবাল (নরমাংসভোজী) শব্দটাও। একসময় নাকি ওরা এমন হিংস্র নরমাংস খেকো এক যোদ্ধা জাতিই ছিল। ডমিনিকায় আসার পরদিনই বদরুজ্জামানের সৌজন্যে কারিবদের এলাকা থেকে ঘুরে এসেছি। ক্যারিবিয়ানের আর দু-একটা দ্বীপে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কিছু কারিব থাকলেও একেবারেই নগণ্য। কারিব যা আছে, তার প্রায় সবই ডমিনিকাতে। ‘কারিবদের এলাকা' বলেছি, কারণ ডমিনিকার উত্তর-পূর্ব উপকূলে প্রায় তিন হাজার ৭০০ একর জায়গা কারিবদের জন্যই সংরক্ষিত। নাম কারিব রিজার্ভ। প্রায় নয় মাইল। রাস্তার দুই পাশে প্রায় সাড়ে তিন হাজার কারিব জনগোষ্ঠীর বাস। এখানকার জমি বাইরের কেউ কিনতে পারে না। কারিবদের বাইরে কারও বসবাস করার অধিকারও নেই।

একসময় নরমাংসভোজী ছিল এমন জংলি এক জাতির সঙ্গে অবশ্য কারিবদের একদমই মেলাতে পারলাম না। বরং একটু পরপর গাড়ি থামিয়ে যাদের সঙ্গে কথা বললাম, সবাইকেই খুব নিরীহ বলে মনে হলো। তবে হ্যাঁ, ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান বলতে আমরা যেমন বুঝি, চেহারা একদমই সে রকম নয়। চ্যাপ্টা নাক, সোজা চুল আর ফরসা গায়ের রং মিলিয়ে অনেকটা আমাদের চাকমাদের মতো। শিশুদের বেশির ভাগের চুল অবশ্য কোঁকড়ানো, যেটিকে বলতে পারেন অন্য জনগোষ্ঠীর সঙ্গে কারিবদের মিশে যাওয়ার প্রমাণ। চাকমাদের সঙ্গে মিল খুঁজে পেলাম আরেকটা ক্ষেত্রেও। হস্তশিল্পে ওস্তাদিতে। পর্যটকদের কাছে বিকোতে রাস্তায় একটু পরপরই ছোট ছোট হস্তশিল্পের দোকান। নানা রকম ঝুড়ি, টুপি, আর ঘর সাজানোর টুকিটাকি এটা-ওটা।
বদরুজ্জামান সাহেবের সঙ্গে দেখি কারিবদের খুব খাতির। কারিবদের একটা পরিবারকে ভালো করে দেখতে চাই বলায় তিনি নিয়ে গেলেন একটা বাড়িতে। গিয়ে হাঁকডাক–এ কই? ও কই? থুত্থুড়ে এক বুড়ি সোফায় (হ্যাঁ, সোফাই) বসিয়ে তাঁর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করতে শুরু করলেন। এক তরুণী টেবিলে বসে ল্যাপটপে ইন্টারনেটে ব্যস্ত। টেলিভিশনের পর্দায় সিএনএন। আমি নিতান্তই হতাশ হলাম। আরে বাবা, এই কি তোদের ঐতিহ্য ধরে রাখার নমুনা! একটু জংলি-জংলি ভাব ধরে রাখবি না!

ঐতিহ্য ধরে রাখা বলতে এখনো কারিবদের গোত্রপ্রধান আছেন। কারিবদের যেকোনো সমস্যায় তিনিই কাজ করেন মুখপাত্র হিসেবে। তবে তাঁরও পরনে চামড়া আর মাথায় পালক-টালক গোঁজা থাকে না। ফিটফাট ভদ্রলোক–স্বচক্ষে অবশ্য দেখিনি, ছবি দেখে বলছি। ডমিনিকার ২১ সদস্যের সংসদে কারিবদের একজন প্রতিনিধি আছেন। সাত না আটজন মন্ত্রী এই দেশে—সেটিরও একটি পদ সংরক্ষিত তাঁর জন্য।
কারিবদের ইতিহাসটা এখানে সংক্ষেপে জানিয়ে দিই। ক্যারিবিয়ানে বসত গাড়া প্রথম মানব প্রজাতি আরওয়াক ইন্ডিয়ান। দক্ষিণ আমেরিকা থেকে ডিঙি নৌকায় করে এখানে পাড়ি জমিয়েছিল ওরা। কারিবরা এসে ডমিনিকার দখল নিয়েছিল আরওয়াকদের মেরে-টেরেই। এসব প্রায় ছয় শ বছর আগের কথা। কারিবরা ডমিনিকার নাম দিয়েছিল 'ওয়েটিকুবুলি', যার অর্থ লম্বা শরীরের একজন। 'ডমিনিকা' নামটা দিয়েছেন ক্রিস্টোফার কলম্বাস। নামকরণের রহস্য, ডমিনিকা আবিষ্কারের দিনটি ছিল রোববার, স্প্যানিশ ভাষায় রোববার হলো ডমিঙ্গো, তা থেকে ডমিনিকা। কলম্বাস তাঁর দ্বিতীয় অভিযানে ১৪৯৩ সালে যখন ডমিনিকায় এলেন, কারিবরা তাঁকে স্বাগতই জানিয়েছিল। কলম্বাস তাঁর প্রতিদান দিয়েছিলেন গণহত্যার বন্দোবস্ত করে। এরপর স্প্যানিশ, ফরাসি, ইংরেজদের সঙ্গে দীর্ঘ যুদ্ধের ইতিহাস। কিন্তু কারিবরা মরতে মরতেও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। এর সবই যে আমার বইপড়া বিদ্যা, এটা বোধ হয় না বললেও চলছে। আমি কি তখন ডমিনিকায় ছিলাম নাকি!
জুলাই ২০০৯। ডমিনিকা।